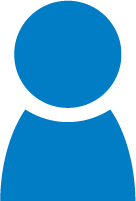বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের আগে দুর্নীতি নিয়ে হৈচৈ একটি প্রচলিত পদ্ধতি। ক্ষমতার পালাবদলের আগে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে হাহাকার হয়। জনগণের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে একটি অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করার একটা চেষ্টা চলে। আন্দোলন বা ষড়যন্ত্র যেভাবেই সরকার বদল হোক, তার আগে দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য সন্ত্রাস ইত্যাদি ইস্যু বড় হয়ে সামনে আসে।
১৯৭৪ সালে সাজানো দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, গণবাহিনীর পরিকল্পিত সন্ত্রাস আগস্ট ট্র্যাজেডির পটভূমি তৈরি করেছিল। এ সময় সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ছিল খাদ্য সংকটের ফুলানো-ফাঁপানো খবর। কালোবাজারি, মজুতদারদের কাহিনি ছাড়া কোনো সংবাদপত্রই প্রকাশিত হতো না। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ’৭৪-এর জানুয়ারি থেকে ’৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি প্রতিটি বক্তব্যেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘বাংলার কৃষক, বাংলার দুঃখী মানুষ—এরা কিন্তু অসৎ নয়। ব্ল্যাক মার্কেটিং কারা করে? যাদের পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা হয়েছে তারাই ব্ল্যাক মার্কেটিং করে। স্মাগলিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া করেছে তারাই বেশি করে। হাইজ্যাকিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া শিখছে তারাই করে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশে টাকা রাখে তারাই।’
১৯৭৫-এর ১৫ জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকব। প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দুর্নীতিবাজদের খতম করব। প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষকে ভালোবাসব।’
কিন্তু সরকারের ভেতরে থাকা দুর্নীতিবাজরা জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দেননি। আর এ কারণেই তিনি তাদের প্রতিহত করার উদ্যোগ নেন। কয়েকজন খারাপ লোক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত করেছিলেন। তাদের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার।
শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজদের ষড়যন্ত্রের কাছেই পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘটে ইতিহাসের বর্বরোচিত নারকীয় ঘটনা। সারা দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ে দেশজুড়ে অস্থিরতা—এমন একটি আবহ সৃষ্টি করেই ’৭৫-এর খুনি, ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করেছিল। আর অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়নি।
১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের আগে দেশে দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কারা বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৮০ সালের শেষ দিক থেকেই শুরু হয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। ১৯৮০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি হয়, ৬ সেপ্টেম্বর দাম বাড়ে গুঁড়া দুধের। ১৮ সেপ্টেম্বর রেশনে চিনির দাম বাড়ে ৫০ শতাংশ, অক্টোবরে নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়ানো হয়। ১৯৮১-এর এপ্রিলে রেশনে চাল ও গমের দাম বাড়ে। লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে স্বৈরাচারের শক্ত শিকলও আলগা হয়ে যায়। ১৯৮০ সালে রংপুর কারাগারে বিদ্রোহ শুরু হয়, পরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন কারাগারে। জিয়া নিহত হওয়ার অল্প দিন আগে ১৯৮১ সালের ৫ এপ্রিল দুর্নীতির দায়ে এক মন্ত্রী ও তিন প্রতিমন্ত্রীকে সরিয়ে দেন। এর পরই ঘটে চট্টগ্রামে সেনা অভ্যুত্থান। ১৯৮১-এর ৩০ মে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান নিহত হন। যেভাবে এবং যে পথে জিয়া ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই পথেই তিনি বিদায় নেন।
জিয়াউর রহমানের বিদায়ের পর ক্ষমতায় আসে বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার। বিচারপতি সাত্তারের সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই শুরু হয় দুর্নীতির নানারকম আলোচনা। দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ আসে বিচারপতি সাত্তারের সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এ সময় ইমদাদুল হক ইমদুর ঘটনায় সরকারের ভিত নড়ে যায়। ইমদাদুল হক ইমদু একসময় জাসদ করতেন। তিনি ঢাকার কালীগঞ্জ থানা গণবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। পরে বিএনপিতে যোগ দেন। কালীগঞ্জে তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অন্ত ছিল না। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সম্পত্তি দখল, অপহরণ, খুনের অভিযোগ ছিল অনেক। যুব উন্নয়নমন্ত্রী আবুল কাশেম সরকারের বাসা থেকে ইমদুকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাশেমের বিরুদ্ধে ইমদুকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনা গোটা সরকারকে বিব্রত করে। একজন মন্ত্রীর বাসায় দাগি খুনি এবং আসামি কীভাবে থাকে, সে নিয়ে হৈচৈ হয়। অনেকে মনে করেন, ১৯৮২ সালে ইমদুর এ ঘটনায় বিচারপতি সাত্তারের সরকারের পতন ডেকে আনে। এর আগে যুবমন্ত্রী কাশেম ১১ ফেব্রুয়ারি সাত্তারের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন। পত্রিকাগুলোয় ইমদুর অপরাধের লোমহর্ষক ঘটনাগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বাড়ে ব্যাপকভাবে। আর এরই ধারাবাহিকতায় পতন ঘটে সাত্তার সরকারের। অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণ করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। দেশে জারি করা হয় সামরিক শাসন। স্থগিত করা হয় সংবিধান।
এরশাদের ৯ বছরের স্বৈরশাসন যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব তার দুর্নীতির আগ্রহ ছিল শুরু থেকেই। সাইকেল চালিয়ে অফিসে গিয়ে তিনি ‘সততা’র প্রমাণ রাখতে চান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করে শুরু করেন দুর্নীতির মহোৎসব। বাংলাদেশের গণমাধ্যম সে সময় শৃঙ্খলিত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এরশাদ সরকারের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় বিদেশি প্রভাবশালী গণমাধ্যমে ‘দরিদ্র দেশের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রপতি’ কিংবা মরিয়ম মমতাজের সঙ্গে এরশাদের প্রেমকাহিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ফেয়ার ফ্যাক্স রিপোর্টে আসে এরশাদের দুর্নীতির আদ্যোপান্ত। চিনি চুরি, গম লুট করে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেওয়া হয় সারা দেশে। উপজেলা পদ্ধতি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে এরশাদ ‘সার্বজনীন দুর্নীতির স্কিম’ চালু করেন। তৈরি হয় উপজেলা টাউট দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী। এ সময় এরশাদের বান্ধবী বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান পত্নী জিনাত হোসেইনের ক্ষমতার দাপট, দুর্নীতি, বিভিন্ন মন্ত্রী এবং এরশাদের একান্ত অনুগতদের অনিয়ম-স্বেচ্ছাচারিতার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে। এমন একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয় যে, জনগণ এরশাদকে একজন দুর্নীতিবাজ এবং লম্পট হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়। ’৯০-এ কুয়েত যুদ্ধের পটভূমিতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ে হুহু করে। সঙ্গে বাড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। দুর্নীতির জন্যই এসব মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। তারা রাজপথে নেমে আসে। স্বৈরাচারের পতন ঘটায়।
১৯৯১ সালে এরশাদের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় আসে নাটকীয়ভাবে। বিএনপি আমলে দুর্নীতির বিভিন্ন খবর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে ড্যান্ডি ডায়িং কেলেঙ্কারি, কোকো লঞ্চ কেলেঙ্কারি, সোনালী ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি, সাইদ ইস্কান্দারের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নিয়মবহির্ভূত ঋণ নেওয়া, সার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নানা দুর্নীতির খবর বিএনপি সরকারকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে। জনগণও বিএনপি সরকারের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দুর্নীতিতে খালেদা জিয়া আর এরশাদ সমান হয়ে যান। খালেদা জিয়ার ভাই-বোনদের দুর্নীতির চর্চা হয় চায়ের আড্ডায়। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপির পরাজয়ের প্রধান কারণ ভোট চুরি আর দুর্নীতি।
১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে দীর্ঘ ২১ বছর পর। আওয়ামী লীগের দেশ পরিচালনার প্রথম দিকের দিনগুলো ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে একটি নতুন উন্নয়নের ধারা সূচনা করেছিল। বিশেষ করে পার্বত্য শান্তি চুক্তি, গঙ্গার পানি চুক্তি বণ্টন, দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাফল্য ছিল অসাধারণ। একটি বাড়ি, একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উন্নয়নের ছোঁয়া পায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে এসে নানারকম দুর্নীতির কেচ্ছা-কাহিনি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে বেশ ফলাও করে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ‘গল্প’ আলোচিত হতে থাকে পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার ছেলের জমি দখল, ঢাকা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এক এমপির অস্ত্র হাতে মিছিলের ছবি। ফেনীতে জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমানের নানারকম খবর গণমাধ্যমে আসতে থাকে রং মাখিয়ে। বিব্রত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। এসব অর্ধেক সত্য, অর্ধেক কল্পিত সংবাদ অনেকে বিশ্বাস করে। এর প্রভাব পরে ২০০১-এর অক্টোবরের নির্বাচনে।
২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে অবশ্য আর অপেক্ষা করেনি। প্রথম দিন থেকেই হাওয়া ভবনের দুর্নীতি সারা দেশে ‘টক অব দ্য কান্ট্রি’-তে পরিণত হয়েছিল। হাওয়া ভবনের মাধ্যমে লুণ্ঠন এবং অনিয়মের এক নজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করে। দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এ সময়। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব অপসারিত হন শুধু দুর্নীতির তথ্য অনুসন্ধান করতে চেয়ে। সরকারি চাকরিতে বদলি-নিয়োগ, টেন্ডার ইত্যাদি সবকিছু দুর্নীতিতে আক্রান্ত হয়। সিএনজিচালিত অটোরিকশা কেলেঙ্কারি, খাম্বা কেলেঙ্কারিসহ হাজারো দুর্নীতির কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকে। বিএনপি অবশ্য এসব মোটেও আমলে নেয়নি, পাত্তাও দেয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার বিএনপি সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। হারিস চৌধুরী, মোসাদ্দেক আলী ফালু, গিয়াস উদ্দীন আল মামুনের মতো দুর্নীতির শিরোমণি দুর্বৃত্তরা জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত হয়েছিলেন এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সরকারই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক—এরকম একটি বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছিল মানুষের মধ্যে। এ সময় বাজারে প্রথম সিন্ডিকেট চালু হয়। সয়াবিন, লবণ কিংবা চিনি বাজার থেকে উধাও করে দাম বৃদ্ধির এক কৌশল শুরু হয়। কারসাজি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ফুঁসে ওঠে মানুষ।
২০০৭ সালে নানা নাটকের পর ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে সেনা সমর্থিত নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণের আগে আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয় দলের নেতাদের দুর্নীতির সত্য-মিথ্যার মিশেলে রগরগে কাহিনি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে। বিশেষ করে বহুল প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোতে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননের এক খেলা শুরু হয়। এই চরিত্র হননের মিশনের মধ্য দিয়েই এক-এগারো সরকার ক্ষমতা দখল করেছিল। রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিবাজ—এটি প্রমাণের চেষ্টা চলে ফখরুদ্দীন সরকারের দুই বছর। এই অনির্বাচিত সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে নিজেরাই দুর্নীতির নেশায় আসক্ত হন। ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেইল করে চাঁদাবাজি, জোর করে অর্থ আদায় সীমাহীন পর্যায়ে চলে যায়। রীতিমতো লুটেরা শাসন কায়েম করেছিল ড. ফখরুদ্দীন-মইন সরকার। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে হুহু করে। পণ্যের বাজারে সৃষ্টি হয় নজীরবিহীন সংকট। গণআক্রোশের আঁচ পেয়ে নির্বাচন দিয়ে কোনোমতে বিদায় নেয় এই সরকার।
টানা চতুর্থবারের মতো সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে আওয়ামী লীগ। দলটি তার নির্বাচনী ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিন্তু পণ্যের বাজারে যেন আগুন লেগেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের সাফল্য নেই এখনো। এর মধ্যে মতি, বেনজীরদের কাহিনি নিয়ে চর্চা হচ্ছে সর্বত্র। তাদের অপকর্মের দায় সরকারের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে। কেউ কেউ এর মাধ্যমে সরকারকেই ‘দুর্নীতিবাজ’ প্রমাণের চেষ্টা করছে। ব্যক্তির দুর্নীতির দায়-দায়িত্ব সরকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়। অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন সরকার এর দায় এড়াতে পারে না। অথচ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হচ্ছে সে ব্যবস্থাগুলো ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে না। কেউ বলছে না, অতীতে কোনো সরকার এভাবে দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিংবা দলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সরকারের শূন্য সহিষ্ণুতা নীতিকে প্রশংসা করা হচ্ছে না। এর ফাঁকফোকর আবিষ্কারে রীতিমতো গবেষণা হচ্ছে। অগণতান্ত্রিক শক্তি বিরাজনীতিকরণের জন্য সবসময় এই পথই বেছে নেয়। আর এ কারণেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এখনই। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে সরকারকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। থাকতে হবে পক্ষপাতহীন। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান যেমন চলবে, তেমনি দুর্নীতির যে কল্পকাহিনিগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তারও উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। কারণ এই উপসর্গ পুরোনো, লক্ষণগুলো ভালো নয়।
লেখক: নির্বাহী পরিচালক, পরিপ্রেক্ষিত
ইমেইল: poriprekkhit@yahoo.com